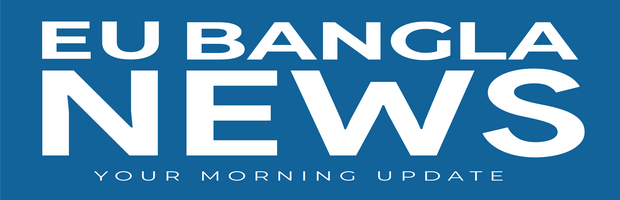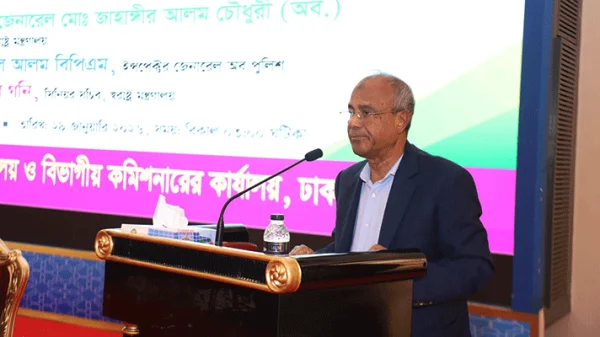সংসদের অনুপস্থিতি সংস্কারে কতটা বাধা

জুলাই অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলোচিত শব্দ ‘সংস্কার’। কিন্তু এই রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি।অন্তর্বর্তী সরকার প্রাথমিক কাজ শুরু করলেও সংবিধানের নীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্ন অবস্থানের কারণে তা বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছে ছয় মাস হলো। সরকার গঠনের পরপরই রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। এর মধ্যে নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, বিচারবিভাগ, জনপ্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশ সংস্কারের জন্য প্রথম দফায় ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই ছয় কমিশন সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।
এরপর ওই ছয় কমিশনের প্রধানদের নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনগুলোর দেওয়া সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে করণীয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঐকমত্য কমিশনের সূচনা বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। এর মধ্যেই নির্বাচনের আগে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব, তা নিয়ে নানারকম মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি মনে করছে সংবিধান পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে হাত দেওয়ার এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার স্বার্থে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু মৌলিক সংস্কারের কাজ শেষ করে জাতীয় নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছে দলটি।
শুধু বিএনপি নয়, অনেক রাজনৈতিক দলই ১৫ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে নিজেদের দলীয় অভিমত জানিয়েছে। তাদের মতে, এই সরকার প্রশাসনিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে যেতে পারেনি। এমনকি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে ব্যর্থতা। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে যে ধরনের প্রশাসনিক দক্ষতা দরকার, তা সরকারের কার্যক্রমে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাই দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সরকার গঠনের পক্ষে মত দেন তারা।
সংস্কার কমিশনগুলোর প্রস্তাবগুলোর কতটুকু বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও সংশয় রয়েছে। এক্ষেত্রে সাংবিধানিক ও আইনি প্রতিবন্ধকতার কথাও আসছে তাদের আলোচনায়।
বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, যেকোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবল নির্বাচিত জাতীয় সংসদের। তবে সংসদ ভেঙে গেলে সংবিধানের বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়, এমন বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রেও প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম অধিবেশনে উপস্থাপন ও উপস্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন দেওয়া না হলে তা আপনা আপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিতে পারিবেন এবং জারি হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোনো অধ্যাদেশে এমন কোনো বিধান করা হইবে না,
(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;
(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়;
অথবা
(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।
(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোনো অধ্যাদেশ জারি হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে। ”
এ অবস্থায় সংস্কারকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার বিষয়টি পরবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর করছে বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরশেদ। বাংলানিউজকে তিনি বলেন, মৌলিক সংস্কার বলতে যেগুলো সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলো সংশোধনের ক্ষমতা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। সেগুলো পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল বা দলগুলোর সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। অন্য যেসব বিষয় আছে সেগুলো রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে করতে পারেন। তবে সেগুলোর জীবনও নির্ভর করবে পরবর্তী সংসদের হাতে। তারা অনুমোদন না দিলে সেগুলোও সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশন শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে আপনাআপনি বাতিল হয়ে যাবে।
এক-এগারো সরকারের জারি করা এমন অধ্যাদেশ অথবা আইনের খসড়াও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার বাস্তবায়ন করেনি উল্লেখ করেন আইনজীবী মনজিল মোরশেদ বলেন, পুলিশ অ্যাক্ট, বিচারক নিয়োগ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে নিয়োগ সম্পর্কিত বেশ কিছু অধ্যাদেশ ও আইনের খসড়া তখন প্রণয়ণ করা হয়েছিল। ২০০৯ সালের পর যারা ক্ষমতায় আসে তারা সেসব অনেক অধ্যাদেশই অনুমোদন দেয়নি।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার একটা গণআন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে। সেক্ষেত্রে তারা যেকোনো সংস্কার করতে পারবে বলে শুরুতে আলোচনা হয়েছে। এখন শুধু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনি জটিলতার কারণে সেই স্পিরিট নষ্ট হয়ে গেল কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে আইনজীবী মনজিল মোরশেদ বলেন, এই সরকার একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় এসেছে ঠিক। তবে এখন আর সেই ইউনিফাইড (ঐক্য) জায়গায় তারা নেই। বিশেষ করে আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা একটি অংশ নির্বাচনকে পাশ কাটিয়েই ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার স্বপ্ন দেখেছে। তাদের রাজনৈতিক অভিলাষ এক্ষেত্রে ঐক্যের জায়গাটাকে নষ্ট করেছে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করা বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত কিছু পদক্ষেপও তাদের বৈধতার জায়গাটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাই বর্তমান বাস্তবতায় যেসব সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামোর বাইরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার মতো অবস্থা আছে বলে মনে হয় না।
মৌলিক সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে প্রায় একই অভিমত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ মাসুমের। বাংলানিউজকে তিনি বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় বড় দল বিএনপির সম্মতি ছাড়া সরকারের পক্ষে বড় রকমের কোনো সংস্কার সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সংস্কারের যেটুকু আশা তৈরি হয়েছিল বর্তমান বাস্তবতায় তা অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। রাজনৈতিক বাস্তবতায় নির্বাচনের পরও যারা ক্ষমতায় আসবে তাদের পক্ষে মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে হয় না। তাই ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে, কিন্তু রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন হবে বলে আমার মনে হয় না।
তবে সংস্কার প্রস্তাবনা কার্যকরের পদ্ধতি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম। বাংলানিউজকে তিনি বলেন, এই সরকারের সংস্কারের কর্তৃত্ব নেই, এমনটা বলা যাবে না। কারণ জনগণের চাওয়াই সবচেয়ে বড় বিষয়। সেক্ষেত্রে প্রথমে সাংবিধানিক পরিষদ বা গণপরিষদের নির্বাচন হতে পারে। তারা সাংবিধানিক সংস্কার করবে। আবার এই সরকার সংস্কার প্রস্তাবনাগুলো গণভোটে দিয়ে অনুমোদন নিতে পারে। সেক্ষেত্রে সাংবিধানিক পরিষদ গঠন সবচেয়ে ভালো অপশন। তারা সংবিধান প্রণয়ন করবে। তারপর নতুন সংবিধানের আলোকে আইনসভার নির্বাচন হবে। তখন আর সেই পদ্ধতির সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সুযোগ থাকবে না।